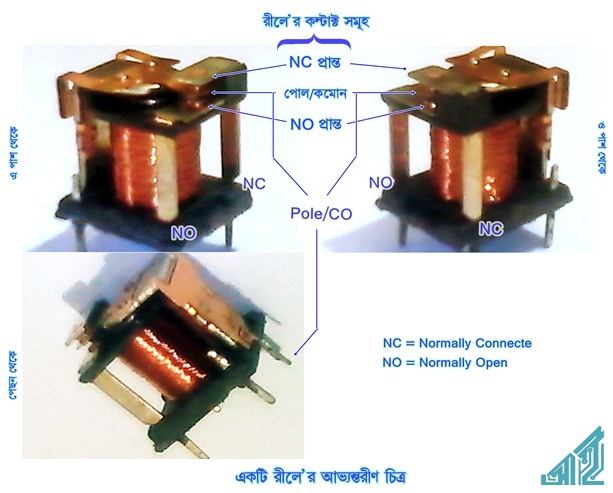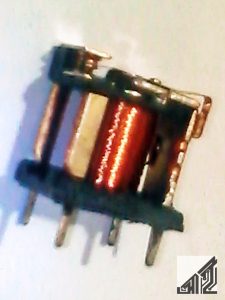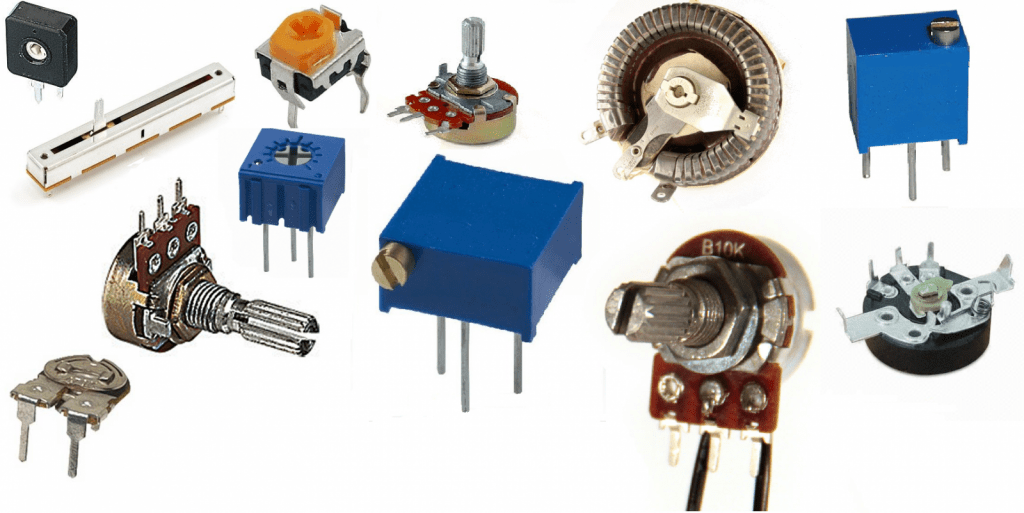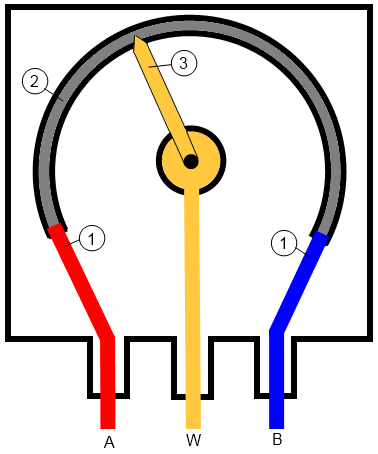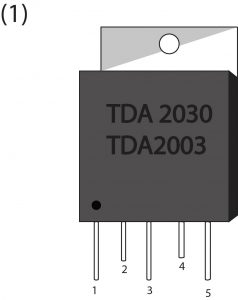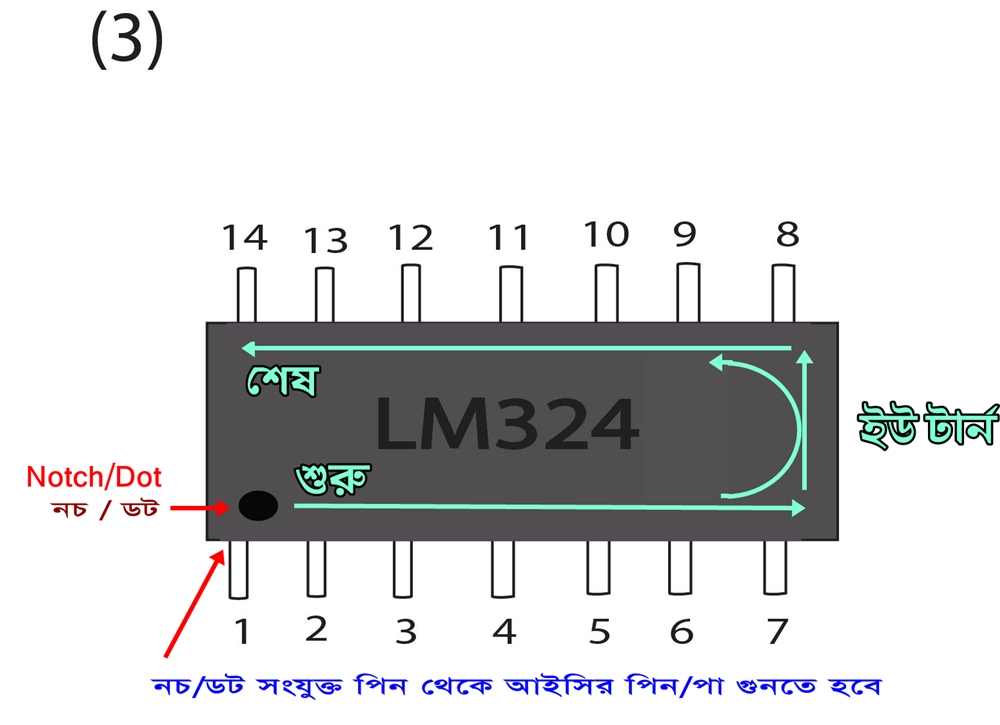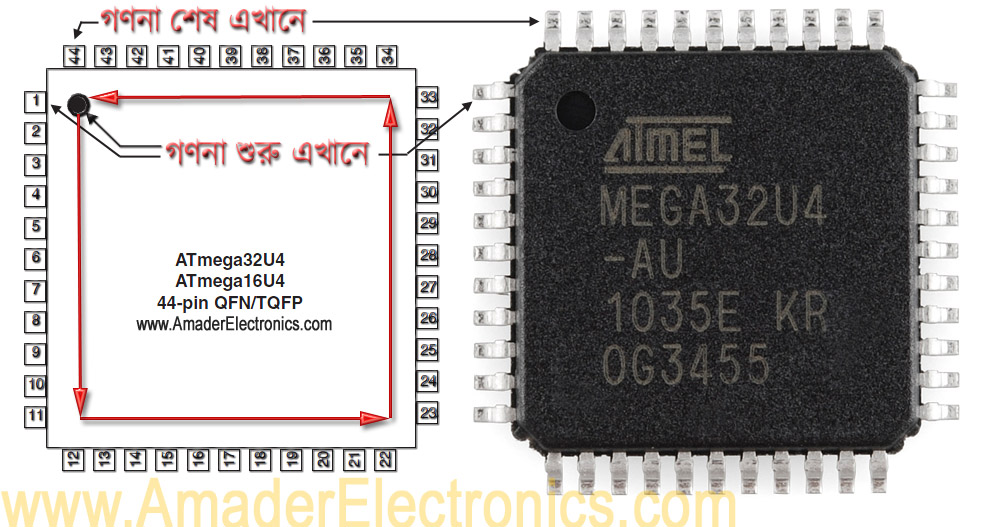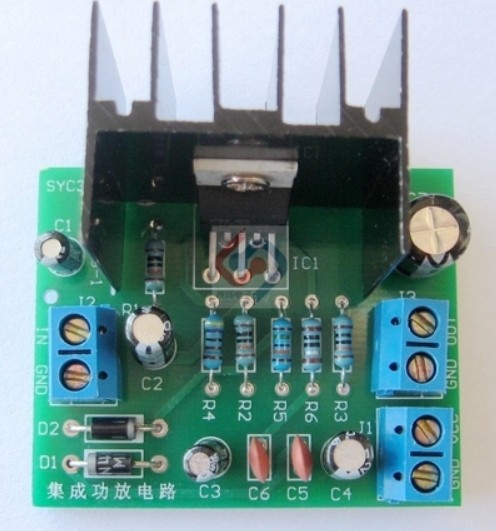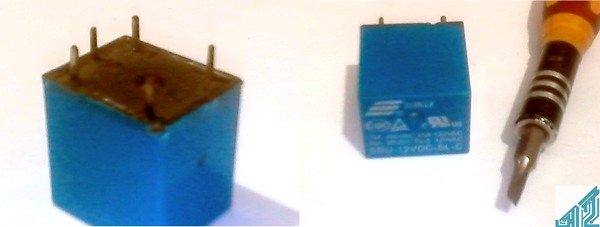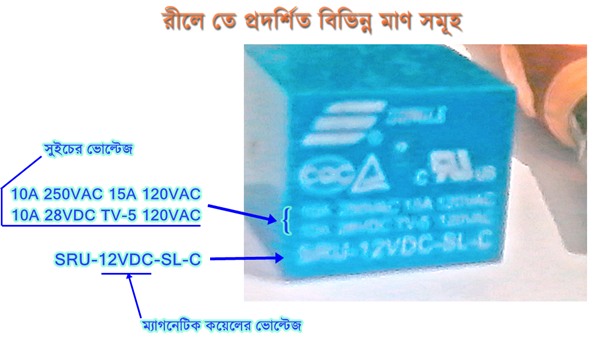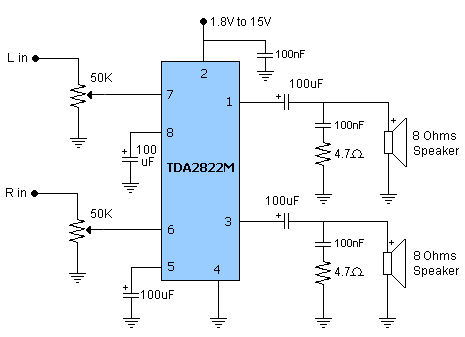বিজ্ঞানের প্রধানতম সৌন্দর্যতা হচ্ছে এর সত্য নিষ্ঠতা। এই সত্য নিষ্ঠতা আসে মুলত প্রমাণ সাপেক্ষে এবং এখানে এই প্রমাণ আসতে পারে দুটো উপায়ে।
১. নির্দিষ্ট পারিপার্শিক অবস্থার প্রেক্ষিতে
২. যে কোন অবস্থার ভিত্তিতে
যেখানে পারিপার্শিকতার প্রভাব থাকে সেখানে ঐ পারিপার্শিক অবস্থা ছাড়া ঐ নির্দিষ্ট প্রমাণ কাজ করবে না এবং এর মানে এই না যে তা সত্যি নয়। আবার যেখানে যে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রমাণ থাকবে সেখানে প্রমাণিত বিষয়টি সকল অবস্থায় একই রকম ভাবে কাজ করবে। একটা মজার বিষয় হলো আমাদের বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলো অধিকাংশই পারিপার্শিকতার উপরই নির্ভর করে। এখানে কিছু বিষয় আগে থেকেই নির্ধারণ করে দিতে হয় তা না হলে সেটা ঠিক ভাবে কাজ করে না। প্রায়োগিক, এপ্লাইড বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ব্যবহার্য জিনিস তা এই নিয়মের আওতায় থেকেই কাজ করে। এর জন্য দেখা যায় যে প্রতিটি জিনিসের একটি ব্যবহার বিধি থাকে যার প্রেক্ষিতে আমাদের ব্যবহার করা জিনিসটি সবথেকে ভালো ভাবে কাজ করতে পারে। একটা উদাহরণ দেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের –
বিজ্ঞান বলেছে যে পানির ঘনত্ব সব চেয়ে বেশী ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। এখন তুমি যদি তোমার বাসার কলের পানি ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ঠান্ডা করে এর ঘনত্ব মাপতে যাও তবে দেখবে এর ঘনত্ব বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত ঘনত্বের সাথে মিলবে না। এর প্রধান কারণ তোমার কলের পানি আসলে বিশুদ্ধ পানি নয়। এর সাথে নানান ধরনের পদার্থ মিশ্রিত। অর্থাৎ পানির ঘনত্ব ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসে বেশী এটা প্রমাণিত বিজ্ঞান হলেও এখানে একটি শর্ত আছে আর তা হলো পানি বিশুদ্ধ হতে হবে। এর রাসায়নিক গুণ ১০০ ভাগ পানির মতো হতে হবে।
তাহলে আগের আলোচনা আর আজকের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে কোন কিছুর বিজ্ঞান হয়ে উঠবার জন্য শর্তাবলী অক্ষুন্ন থাকা অত্যাবশকীয়। এই অত্যাবশকীয় শর্তাবলী না মানলে প্রমাণিত জিনিসও কাজ করবে না সঠিক ভাবে। সেই সাথে এটাও জানা হলো কোন বিজ্ঞানীর আবিস্কার করা কোন নিয়মকে কাজে লাগাতে হলে নির্দিষ্ট শর্তাবলী পালন করতে হবে নিয়ম মেনে।
এ্ই নিয়মের মাঝে একটা নিয়ম এখন আমরা জানবো আর সেটা হলো শক্তির কোন ধ্বংস নাই – শক্তি এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থাতে শুধু রুপান্তরিত হতে পারে। সেই সাথে শূণ্য থেকে কোন শক্তি যেমন তৈরী হতে পারে না তেমন করেই কোন শক্তি শূণ্যে মিলিয়ে যেতে পারে না। এ্টা হলো শক্তির নিত্যতা সুত্র। তাহলে যদি শক্তি নতুন করে তৈরী হতে না পারে এবং শক্তি শেষ না হয় কখনো তবে আমাদের ভাবায় যে এই মহাবিশ্বের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট শক্তি একটি স্থির অবস্থানেই আছে। এর শুধু মাত্র রুপান্তর হয়েছে বা হচ্ছে। আমরা এই পৃথিবীতে এই শক্তি রপান্তরের বিভিন্ন যন্ত্র তৈরী করে আমাদের গাড়ী, বিদ্যুত সহ নানান যন্ত্র চালাচ্ছি। এই রুপান্তরের প্রকৃয়াতে যে শক্তি আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারছি না তা শক্তির অপচয় বলছি আমরা।
বিভিন্ন সময় আমরা এখন দেখতে পাই যে, জ্বালানী বিহীন বিদ্যুত উৎপাদনের খবর আসছে বিভিন্ন পত্রিকার পাতায়। ইন্টানেটে ঘাটলে তোমরা দেখবে যে ভিডিও আছে এই সব যন্ত্রের। অনেকে তা বিশ্বাসও করে। তোমরা কি বিশ্বাস করবে এমন যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব? আসলেই কি এমন কোন যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব যাতে কোন প্রকার শক্তি না দিয়ে শক্তি পাওয়া যাবে!! শক্তির নিত্যতা সূত্র মেনে কি এটা আদৌ সম্ভব? বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে এখানে আমরা চিন্তা করলাম জ্বালানী বিহীন বিদ্যুৎ তৈরী করা সম্ভব কিনা এবং করলে কিভাবে আর না হরে কেনো নয়? চিন্তা ও প্রশ্ন তো হলো – এবার আসো আমরা দেখি প্রমাণ কি বলে –
তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে প্রতিটি এই ধরণের যন্ত্র একটি প্রাথমিক পাওয়ার সোর্স বা শক্তির উৎস ব্যবহার করে – সেটা ব্যাটারী, হাতের ধাক্কা বা চুম্বক শক্তি হতে পারে কিন্তু কিছু না কিছু থাকেই। এর পর দাবী করা হয় এটা এভাবেই চলতে থাকবে আজীবন ধরে কখনো এই যন্ত্র থামবে না। কিন্তু বিজ্ঞান বলে এই যন্ত্র প্রাথমিক শক্তির রুপান্তরের পরই থেমে যাবে। এখানে শর্তাবলী হলো এই যন্ত্র এমন এক মাধ্যমে চলছে যেখানে বাতাস আছে যার বাধা তৈরী করবার ক্ষমতা আছে, এই যন্ত্রের সাথে যুক্ত বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সাথে এর ঘর্ষণ আছে যা বাধা তৈরী করবে, আর ঘর্ষণ মানেই হলো তাপ উৎপাদন অর্থাৎ গতি শক্তি কে তাপ শক্তিতে রুপান্তর, প্রাথমিক যে শক্তি দেওয়া হচ্ছে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। এখন এই যন্ত্রের প্রাথমিক অবস্থার পর থেকেই এর প্রাথমিক শক্তি রুপান্তরিত হতে থাকবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর যা নির্ভর করবে প্রাথমিক শক্তির পরিমানের উপর এই যন্ত্রে আসলে আর কোন শক্তি থাকবে না অর্থাৎ এই যন্ত্র থেমে যাবে।
রুপান্তুরিত শক্তিকে যদি এর প্রাথমিক শক্তির দিকে চালিত করা হয় অর্থাৎ এর আউটপুটকে যদি ইনপুটে দেওয়া যায় তবে এই শক্তির চলমান সময় বেড়ে যাবে। কিন্তু তাতে করে এর বাতাসের সাথে বাধার অপচয়, ঘর্ষণের ফলে শক্তির রুপান্তর এই সব শর্ত শিথিল হবে না। এর ফলে এই অপচয়ের শক্তি টুকু কখোনোই আর যুক্ত হবে না এর প্রাথমিক উৎসের সাথে। এতে করে যখন এর অপচয়কুত শক্তি ও এর প্রাথমিক শক্তির পরিমাণ এক হবে তখন এই যন্ত্র আর কাজ করবে না। এই ধরণের যন্ত্র পারপেচুয়াল মেশিন নামে পরিচিত। তাহলে আমরা এটা শিখলাম যে জ্বালানী বিহীন বা প্রতিনিয়ত সরবরাহকরা শক্তি বিহীন কোন যন্ত্র আজীবন চলতে পারবে না যা শক্তির নিত্যতা সুত্র দ্বারা নির্ধারিত এবং শক্তির রুপান্তরের কারণে বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।